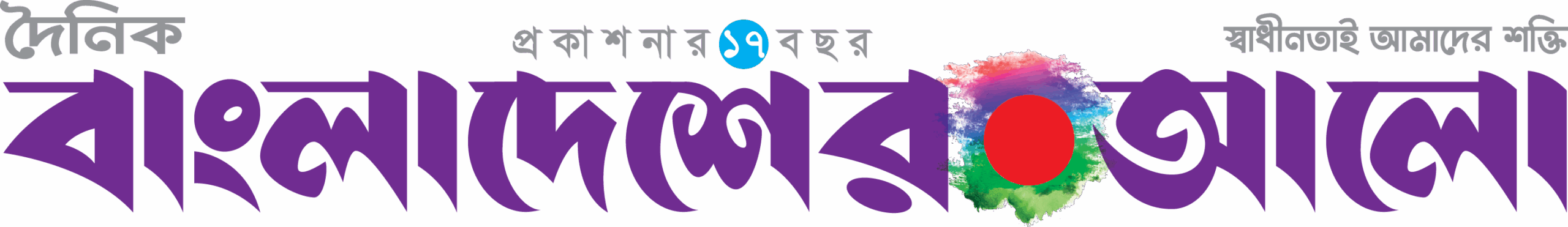নদীর খেয়ালে জীবনের লড়াই: বাংলাদেশে নদীভাঙণের করুণ বাস্তবতা
dailybangla
31st Aug 2025 2:33 pm | অনলাইন সংস্করণ
আল শাহারিয়া
ভাবুন তো এমন একটি চিত্রপট, আপনি একটি বাড়ি বানালেন। পুকুরভরা মাছ, গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গবাদিপশু নিয়ে সুখেই কাটছে জীবন। অতঃপর একদিন আদেশ এলো সব ছেড়ে দিতে হবে। সব মানে সব, পায়ের নিচের জমিটাও।
অবাক হচ্ছেন? আসলে অবাক হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। এটা বাংলাদেশের নদীতীরবর্তী জীবনের স্বভাবিক ঘটনা। এই নদীভাঙন কত বিত্তশালী মানুষকে রাস্তায় নামিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নদীভাঙনের শিকার হলে আসলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আপনি সর্বোচ্চ আপনার জীবনটা হাতে নিয়ে সরে পড়তে পারবেন, সেটাও অনেকসময় হয়ে ওঠে না। এমন অনেক জনশ্রুতি পাবেন যে, ঘুমের মধ্যে নদীর মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি সহ গোটা পরিবার৷
প্রকৃতির খেয়ালই নদীভাঙনের প্রধান কারণ। বর্ষায় যখন উজান থেকে পাহাড়ি ঢল নেমে আসে, তখন প্রবল স্রোতের ধাক্কায় নদীর তীর ক্ষয় হতে থাকে। অতিবৃষ্টি আর বন্যা এই ক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করে। কোথাও পলি জমে নদী অগভীর হয়ে যায়, আবার কোথাও সেই স্রোত তীরের সবকিছু গ্রাস করে ফেলে। কখনও কখনও ভূমিকম্প বা ভূমির স্বাভাবিক পরিবর্তনে নদীর গতিপথ বদলে যায়। তখন হঠাৎ করেই নতুন নতুন জায়গায় ভাঙন শুরু হয়। আর নদীর নিজস্ব চরিত্র পরিবর্তনশীল, সুযোগ পেলে সে তার গতিপথ বদলায়। কখনও এর বুকে নতুন চরের জন্ম দেয়, আবার পুরোনো চরকে গ্রাস করে নেয়।
কিন্তু, দায় কি শুধুই প্রকৃতির? না। মানুষের অব্যবস্থাপনাও নদীভাঙন বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ তৈরি কিংবা চর দখল নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যাহত করছে। অনেক সময় একপাশে বাঁধ দিয়ে ভাঙন ঠেকানো হয়, অথচ সেই পানির চাপ যখন অন্য তীরে পড়ে তখন সেখানেই শুরু হয় নতুন ভাঙন। পাহাড় কেটে মাটি ফেলা বা বন উজাড়ের কারণে নদীতে পলির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ভারসাম্য নষ্ট হয়। নিয়মিত ড্রেজিং না হওয়ায় নদী আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও যুক্ত হয়। অনিয়মিত বৃষ্টি ও ক্রমাগত হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে নদীর উপর চাপ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।
নদীভাঙনের আসলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দু’রকম প্রভাবই রয়েছে।
নদীভাঙন এর সাথে সবচেয়ে পরিচিত শব্দ হলো অভিবাসন। আপনি যখন পায়ের নিচের মাটিটাও হারাবেন, আপনাকে নতুন ভূমির সন্ধান করতেই হবে। একে বাধ্য অভিবাসন বলা হয়(forced migration)। কেউ আবার ভূমি হারানোর আগেই এই অনুসন্ধান সেরে নেয় এবং নতুন জায়গায় বসতি গড়ে। এই অভিবাসন পারিবারিক দূরত্ব বাড়ায়, ফলত সামাজিক বন্ধনে অনেকটাই ভাটা পড়ে। অর্থাৎ, নদীভাঙনের সামাজিক ক্ষতি মানে শুধু স্থানচ্যুতি নয়; এটি মানুষের পরিচয়, মর্যাদা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পর্ক ও নিরাপত্তাকে গভীরভাবে আঘাত করে।
অর্থনৈতিক দিক থেকেও ক্ষতি অনিবার্য। নদী গ্রাস করে নেয় উর্বর কৃষিজমি। ফলত কমে যায় ফসল, ধ্বংস হয় কৃষকের জীবিকা। একইসাথে বিলীন হয় কৃষকের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, ফলের বাগান, মাছের ঘের। সমস্ত সম্পদ ও আশ্রয় হারিয়ে মানুষ শহরে গিয়ে শুরু করে দিনমজুরি, রিকশা চালানো বা ইটভাটার কাজ। আবার কেউ কেউ চুক্তিভিত্তিক ইটভাটায় কাজ নেয় নির্দিষ্ট মৌসুমে। একবার দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়লে আর বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। নতুন করে বসতি গড়ার খরচও অনেক সময় জোটে না। সরকারি এবং দেশী-বিদেশী এনজিও’র সাহায্যও এদেশে অপ্রতুল। স্থানীয় অর্থনীতি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। নদীভাঙনে বিলীন হয় স্থানীয় স্কুল, হাটবাজার, রাস্তাঘাট। যার ফলে বাজারে খাদ্যের দাম বেড়ে যায়। যা সরাসরি জীবনের স্বাভাবিকতার উপর প্রভাব ফেলে।
নদীভাঙনের প্রভাব আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তীব্র। উপকূলীয় নদীভাঙন ‘লবণাক্ততা’ নামের আরেকটি নতুন সমস্যাকে ত্বরান্বিত করে। বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে নদীর দূষিত এবং লবণাক্ত পানি লোকালয়ে প্রবেশ করে। এটি আবার সরাসরি প্রভাব ফেলে সমাজ এবং অর্থনীতিতে। হুমকির মুখে ফেলে খাদ্য নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে।
তবুও নদীভাঙনকে পুরোপুরি থামানো না গেলেও এর ক্ষতি কমানো সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় বাঁধ, স্পার, জিও ব্যাগ ব্যবহার কিংবা নিয়মিত ড্রেজিং নদীকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে আগাম সতর্কীকরণ, পুনর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা কার্যকর করা জরুরি। নদীতীরবর্তী পরিবারকে আশ্রয়ন প্রকল্পে নিরাপদ আবাসন দেওয়া, বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান তাদের জীবনে নতুন আলো জ্বালাতে পারে। একই সাথে দরকার পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ। যেমন নদীর তীরে বনায়ন, প্রাকৃতিক প্রবাহকে অবরুদ্ধ না করা এবং নদী দখল রোধ করা।
শিক্ষার্থী
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
বিআলো/ইমরান