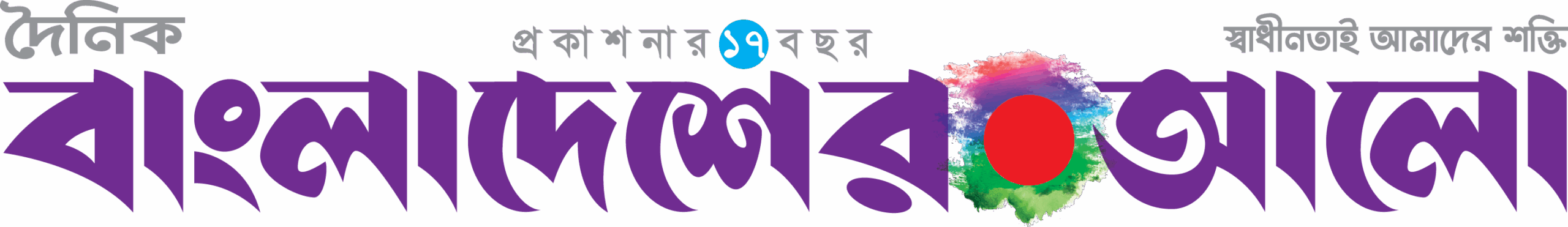স্নাতক ডিগ্রিধারীদের বেকারত্বের চাপ
৮ বছরে শিক্ষিত বেকার দ্বিগুণ ,প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন স্নাতক
রতন বালো: িউচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা মানেই কি চাকরি খোঁজা? শিক্ষিত হওয়া মানেই কি সরকারি, কর্পোরেশনের কিংবা অন্যের অফিসে চাকরি করা? এমন প্রশ্ন নিয়েই দেশে বাড়ছে বেকারত্বের চাপ। যদিও দেশের বেকারদের ভিতরে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে উচ্চশিক্ষিত যুবক। অবশ্য তারা মেধাবী এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়ে। সে তুলনায় স্বল্প শিক্ষিত মানুষের ভিতরে বেকার সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম। এই বিশাল বেকার রাষ্ট্রের জন্য যেমন বোঝা, তেমনি সামাজিক অবস্থানে তারা অনেকটাই নৈরাজ্যের শিকার।
হ্যাঁ যদিও এটি সত্য যে, শিক্ষিত হওয়া কিংবা উচ্চশিক্ষিত হওয়া মানে বিশেষ কিছু দক্ষতা অর্জন করা (মানবিক তো বটেই) যা দ্বারা তারা দেশি, বিদেশি কোনো সংস্থায় সার্ভিস দিয়ে অর্থ উপার্জন করা, যা দ্বারা নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করা হয়।
দেশে বিসিএসে মাত্র কয়েক হাজার পোস্ট অথচ প্রতিবছর হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার্স পাস করা শিক্ষার্থী বের হন, সবাই যদি সরকারি চাকরি খোঁজেন তাহলে জায়গা কোথায়? এদিকে দেশের উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণিটি গোলামির জন্য চাকরি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। তার কারণ, নিজের উপর আস্থার সংকট, পাশাপাশি নিশ্চিত মাসিক আয়ের উৎস খুঁজে নেওয়া। বিগত ৮ বছরে শিক্ষিত বেকার দ্বিগুণ, প্রতি তিনজন বেকারের একজন স্নাতক। আবার দীর্ঘদিন বেকার থাকা তরুণদের মধ্যেও স্নাতকদের হার বেশি। দুই বছরের বেশি সময় ধরে যারা কাজ পাচ্ছেন না, তাদের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রিধারীরাই সংখ্যায় শীর্ষে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। তাতে দেখা যায়, শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি এবং দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্বের প্রবণতাও বেশি। দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত তরুণ-তরুণী হয় একেবারেই চাকরি পাচ্ছেন না, নয়তো পছন্দমতো কাজ পাচ্ছেন না। ফলে তারা বেকার হয়ে হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন। এই সব বেকারের একটি বড় অংশ মেসে থেকে মানবেতর জীবন যাপন করছেন, একটি সম্মানজনক চাকরির অপেক্ষায় দিন গুনছেন। আবার মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত তরুণরা পরিবারের সঙ্গেই থাকেন, কিন্তু নানা টানাপোড়েন ও মানসিক চাপ তাদের অসহায় করে তুলছে।
মেধাবীদের মধ্যে বেকারত্ব বেশি। কি এর কারণ? বিআইডিএসের গবেষণা অনুযায়ী, সার্বিকভাবে শিক্ষিতদের মধ্যে ৩৩ শতাংশের বেশি বেকার। আর এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যারা প্রথম শ্রেণি পেয়েছে, তাদের মধ্যে বেকারত্ব ১৯ থেকে সাড়ে ৩৪ শতাংশ। বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশই বেকার। স্নাতক পর্যায়ে এমন মেধাবীদের বেকারত্বের হার প্রায় ২৮ শতাংশ।
এদিকে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া প্রতি তিনজনের একজনই বেকার বসে আছেন। আর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ-৫ পাওয়াদের মধ্যে ৩১ শতাংশের বেশি বেকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী, কাজপ্রত্যাশীদের মধ্যে সপ্তাহে ন্যূনতম এক ঘণ্টা মজুরির বিনিময়ে কাজের সুযোগ না পেলে বেকার হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশে এমন বেকার ২৭ লাখ। বিআইডিএসের গবেষণায় বলা হয়েছে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণি পেয়েও চাকরি মেলে না।
বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ২৪ হাজার। এর মধ্যে ৮ লাখ ৮৫ হাজারই স্নাতক ডিগ্রিধারী। সার্বিকভাবে গত কয়েক বছর ধরে বেকারের সংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। এখন প্রতি তিনজন বেকারের একজনই উচ্চশিক্ষিত, যারা বিএ বা এমএ ডিগ্রি নিয়েও শোভন চাকরি পাচ্ছেন না।
২০১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গিয়েছিল, তখন দেশে চার লাখের মতো স্নাতক বেকার ছিলেন। আট বছর পর এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় নয় লাখে, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত বেকার দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে ১৭ শতাংশের বেশি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বেকার রয়েছেন। উচ্চমাধ্যমিক পাস করা তরুণদের ক্ষেত্রে এ হার ৮ শতাংশের বেশি। আর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন তরুণদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব মাত্র ১ শতাংশ।
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বেকারের সংজ্ঞায় বলছে, কেউ সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করে মজুরি পেলে তাকে বেকার ধরা হবে না। কেউ এক মাস ধরে কাজ প্রত্যাশী এবং সর্বশেষ এক সপ্তাহে যদি এক ঘণ্টাও মজুরির বিনিময়ে কাজ করার সুযোগ না পান, তবেই তাকে বেকার হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করে জীবনধারণ অসম্ভব। এ ছাড়া প্রায় এক কোটি মানুষ আছেন, যারা পছন্দসই কাজ পাচ্ছেন না। তাদের ছদ্মবেকার বলা হয়।
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, হতাশার বিষয় হল মাস্টার্স পাস করেও দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি না পাওয়া। পছন্দমতো চাকরি তারা পাচ্ছে না কিংবা বাজারে যে ধরনের চাকরি আছে, সেই ধরনের ডিগ্রি তাদের নেই। এতে সমাজ ও সরকার যে বিনিয়োগ করল, সেটা কাজে লাগল না। এভাবেই শিক্ষিত শ্রমশক্তির অপচয় হচ্ছে।
গবেষণা প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী চাকরিজীবীদের মধ্যে মাত্র ২৫ দশমিক ৪৯ শতাংশের বেতন চল্লিশ হাজার টাকার বেশি। এমন মেধাবীদের মধ্যে আবার দশ শতাংশ মাসে দশ হাজার টাকাও বেতন পান না। বাকি ৬৫ শতাংশ মেধাবীর বেতন দশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে। স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়েছেন, এমন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেতন দশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে।
স্নাতকে প্রথম শ্রেণি পাওয়া ২৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ ডিগ্রিধারী চল্লিশ হাজার টাকার বেশি বেতন পান। এ ধরনের ৭০ শতাংশ মেধাবীর বেতন দশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে। আর ৫ শতাংশ তো মাস শেষে দশ হাজার টাকাও পান না। স্নাতক পর্যায়ে সিজিপিএ পদ্ধতিতে সাড়ে তিন শতাংশের বেশি স্কোরধারীদের প্রায় ৩৯ শতাংশের বেতন চল্লিশ হাজার টাকার বেশি। সিজিপিএ সাড়ে তিনের বেশি স্কোর করা ৪৫ শতাংশ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ৪০ হাজার টাকার বেশি বেতন পান।
এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, শিক্ষাজীবনের প্রথম শ্রেণি বা ভালো রেজাল্ট চাকরির বাজারে বেতন বেশি পাওয়ার জন্য একমাত্র নিয়ামক নয়, তবে চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণি পাওয়া মেধাবীরা এগিয়ে থাকেন। কিন্তু চাকরিতে তিনি কেমন করছেন, কতটা দক্ষ হয়েছেন- সেটাই পরবর্তী সময়ে বেতন-বৃদ্ধির নিয়ামক হয়ে যায়। তিনি অবশ্য বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রথম শ্রেণি পাওয়া মেধাবীরা বেশি বেতনের চাকরি পাবেন এবং তাতে সফল হওয়ার ব্যাপারে খুব আশাবাদী থাকেন। কিন্তু পরে বাস্তবতার সামনে পড়ে তারা হতাশ হন।
বিআলো/ইমরান