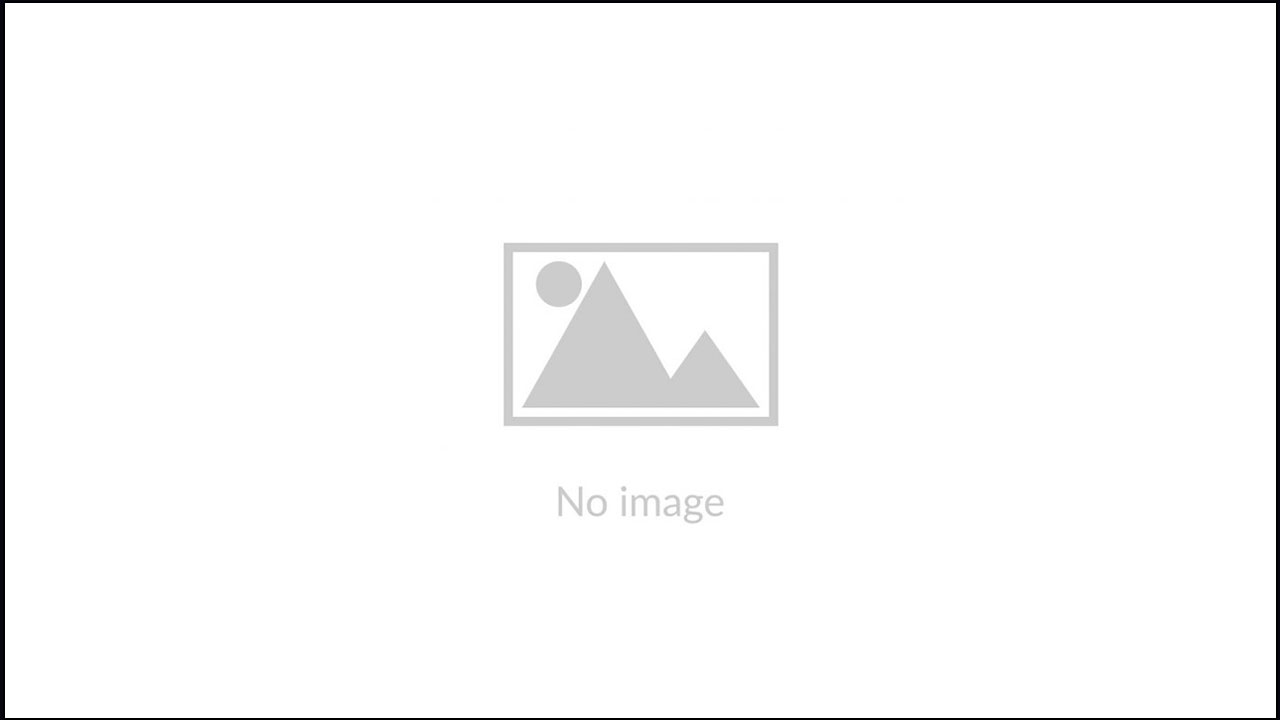ভারতের নির্বাচন শুধু জয়-পরাজয়ে আটকে নেই
সাইমন মোহসিন: ২০২৪ সালটা বিশ্বব্যাপী নির্বাচনে ব্যস্ততম বছর। আর এই ব্যস্ততার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসরগুলোর একটি হলো ভারতের নির্বাচন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের এই নির্বাচন নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতে ভোটার রয়েছে প্রায় ৯৭ কোটি। আজ থেকে প্রায় দেড় মাস ধরে চলবে এই নির্বাচন আয়োজন। এই নির্বাচনের মূল বিষয়বস্তু এখন আর জয়-পরাজয়ে আটকে নেই, বরং
নির্বাচনটা সুষ্ঠু ও অবাধ হবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। নির্বাচনের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে ধর্ম বনাম সুশাসনের লড়াই। এই নির্বাচনের কেন্দ্রীয় আলোচনা নির্বাচনী ও জাতীয় ইস্যু নয়, বরং কে এই নির্বাচনের মূল চরিত্রের ভূমিকা রাখছেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।
৭৩ বছর বয়সী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সোপান ধরে ভারতের ক্ষমতায় আসীন হন। তবে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিনি ধর্ম ও রাজনীতি একাকার করে দিয়েছেন। তাঁর এই পন্থা দেশের হিন্দুত্ববাদীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি করলেও দেশে এখনো প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ণ বাস্তবায়নে ব্যর্থ। মোদির নেতৃত্বে বৈশ্বিক পর্যায়ে ভারতের প্রভাব ক্রমবর্ধমান হলেও, দেশের অভ্যন্তরে বেকারত্বও সমানতালে বেড়ে চলেছে। জাতিগত সহিংসতা, বিশেষ করে মুসলিমদের ওপর হিন্দুত্ববাদীদের হামলা ও অত্যাচারের ঘটনা যেমন বেড়েছে, তেমনি গণমাধ্যম, বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে।
এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া নিয়ে শঙ্কার কোনো শেষ নেই। সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীগুলোর পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এবং নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাওয়াটা নির্বাচনের অবাধ ও সুষ্ঠুতার প্রশ্ন আরো প্রকট করেছে। নির্বাচনের এত কাছে এসে বিরোধী আম আদমি পার্টির প্রধান ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে দুর্নীতির অভিযোগে আটক করার বিষয়টা সবচেয়ে দৃষ্টিকটু হয়েছে। বিজেপির এমন আচরণ অবশ্য নতুন নয়।
সেই ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিরোধী দল কংগ্রেস সদস্যদের এবং যেসব প্রদেশে বিজেপি ছাড়া অন্য দল ক্ষমতায়, সেসব দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে সরকারি কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানী এজেন্সিগুলোর দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান ও প্রমাণের প্রচেষ্টার কোনো কমতি নেই। আর এই প্রচেষ্টার লক্ষ্যই হলো ২০২৪ সালের নির্বাচনকে মোদি ও বিজেপির জন্য যথাসম্ভব অপ্রতিযোগিতামূলক আয়োজনে পরিণত করা। তা ছাড়া বেশ কয়েক বছর আগের আয়কর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ভুলত্রুটির সুবাদে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অর্থ আয়কর বিভাগের আটক করে রেখে দেওয়াটাও অনেকটা একই লক্ষ্য ও অভিসন্ধি প্রকাশ করে। আর ভারতের স্বনামধন্য নির্বাচন কমিশনও এখন তার নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন।
এখানে বলতে হয়, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের কাছে এই বিষয়টা সর্বাধিক অবাক করা ও দৃষ্টিকটু। কারণ ভারতের নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা, নিরপেক্ষতা ও মৌলিকতা নিয়ে সবারই বরাবর বেশ ইতিবাচক ধারণা, কিন্তু এবার তাতেও ব্যাঘাত ঘটেছে। নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য হঠাৎ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই পদত্যাগ করার পরপরই বিজেপি সরকার রীতিমতো তড়িঘড়ি করে কমিশনে দুজন নতুন সদস্য নিয়োগ দেয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে আলোচনা, সমঝোতা ও সমন্বয়ের পন্থাগুলো সঠিকভাবে অবলম্বন না করারও অভিযোগ রয়েছে। তাই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক! শুধু তা-ই নয়, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) নিয়েও প্রশ্নের শেষ নেই। ইভিএমের হিসাব নির্ণয়, নিরূপণ ও নিরীক্ষার পাশাপাশি কাগজে কোনো হিসাব থাকবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ইভিএমে কোনোভাবেই কোনো কারচুপির সুযোগ নেই- সরকার এমন দাবি করলেও, সেটা জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। আর এই বিষয়টা আরো ঘোলাটে হয়ে আসে, যখন জানা যায় যে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে রাজিই হয়নি।
মোদি শাসনের কিছু ভালো দিকও রয়েছে। বিশ্বপরিসরে ভারত এখন এক প্রভাবশালী পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশের অর্থনীতির আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। দেশের স্টক মার্কেটের ব্যাপ্তি তিন গুণ হয়েছে। কিন্তু এসবের সুবিধা ও সুফল উপভোগ করছে সমাজের উচ্চশ্রেণি এবং বিদেশে বসবাস করা সচ্ছল অনাবাসিক ভারতীয়রা, যাদের বেশির ভাগই আবার দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী। এখনো ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের বার্ষিক আয় তিন হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারের নিচে। মোদি সরকারের অধীনে অনেক সমাজকল্যাণমূলক সরকারি কর্মসূচি চালু হয়েছে, যার ফলে প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে জীবনধারণ অনেকটা সহনীয় এখন। কিন্তু সেটা আবার সরকারি টাকশালে যেমন চাপ ফেলছে, তেমনি কর্মসংস্থান উন্নয়নে অকার্যকর।
মোদির বিজেপি প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, হিন্দুত্ববাদী শক্তি, অনাবাসিক ভারতীয়দের মধ্যে জনপ্রিয়তা ইত্যাদির ওপর ভর করে লড়ছে। অন্যদিকে প্রায় ২৮টি বিরোধী দল একজোট হয়ে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই দলগুলোর নিজস্ব এজেন্ডা, ইস্যু, নির্বাচনী ইশতেহারের লক্ষ্য ও মানদণ্ডে ভিন্নতা থাকতেই পারে। তবে একটি বিষয়ে তারা একাট্টা। তারা মনে করে, তৃতীয়বারের মতো মোদি ও বিজেপিকে সরকার গঠন থেকে থামাতে হবে। নতুবা ভারতে গণতন্ত্রের মৃত্যু হবে। এই মহাজোট নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগির বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে একটা সমঝোতায় আদৌ আসতে পারবে কি না, সেটা পরের বিষয়। আপাতত তারা মোদির বিরুদ্ধে আরো কিছু অভিযোগ ও ইস্যু নিয়ে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত। এককভাবে হয়তো এই দলগুলো বিজেপির জন্য কোনো সমস্যা নয়। তবে
একাট্টা হয়ে তারা বিজেপির জন্য বিপদ বয়ে আনতে পারে। কারণ প্রতিটি দলের কাছেই ভোট ব্যাংক এবং মোদি ও বিজেপির ব্যর্থতা, অন্যায় কিংবা স্বেচ্ছাচারিতার যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে, যা স্থানীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিজেপির নেতাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
বিরোধী দলের সবচেয়ে যে সমস্যা, সেটা হলো মোদিবিরোধী এজেন্ডা ছাড়া আর তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি নেই তাদের। মোদির ব্যর্থতা ও অন্যায়কে সঠিক করার প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল। এ জন্যই বিজেপি মোদির বিজয় নিয়ে অতটা আত্মতুষ্টি ও আত্মবিশ্বাসী নয়, যতটা গত বছরও থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। এ জন্যই কেজরিওয়ালকে আটকের পর বিরোধী দলগুলোর শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অনুষ্ঠান উপর্যুপরি শক্তির প্রয়োগে বন্ধ করা হয়েছে। মোদি ও বিজেপির বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেন কোনো পোস্ট বা বক্তব্য সহজে প্রকাশ না পায় তার জন্য সরাসরি ফেসবুকের মালিক মেটার সঙ্গে সমঝোতাও করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন অভিযোগও শোনা যাচ্ছে যে মোদি ও বিজেপির সমালোচনা করে বক্তব্য ও পোস্ট দিলেই তা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে কিংবা সামাজিক মাধ্যমের গ্রুপগুলোতে নীতির বিরোধী বলে সেগুলো আর প্রকাশিতই হচ্ছে না। যুক্তিসংগতভাবেই সামাজিক মাধ্যম এখন রাজনৈতিক খেলায় এক কার্যকর হাতিয়ার। সেটাকেও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। আর যার ফলে বাকস্বাধীনতা, গণমাধ্যম ও ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধার বিষয়টা আরো প্রকটরূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। বিষয়টা এখন এতটাই প্রকট যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও তার সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলেছে যে বিজেপি সরকারের অসহনশীলতা এখন চরম মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এসবই বিজেপির অস্বস্তি ও আত্মবিশ্বাসের অভাবকে তুলে ধরে।
লেখক : রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক
বিআলো/শিলি